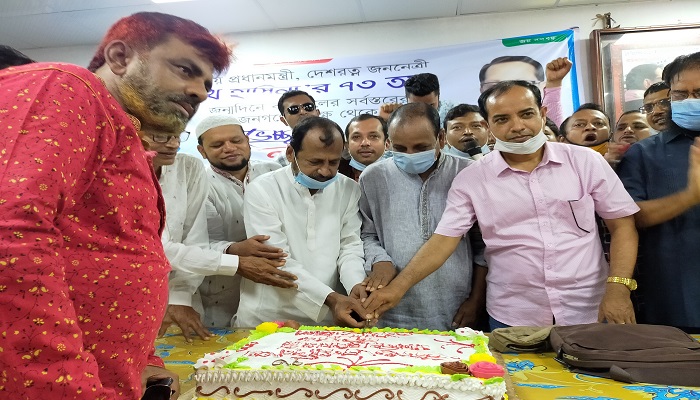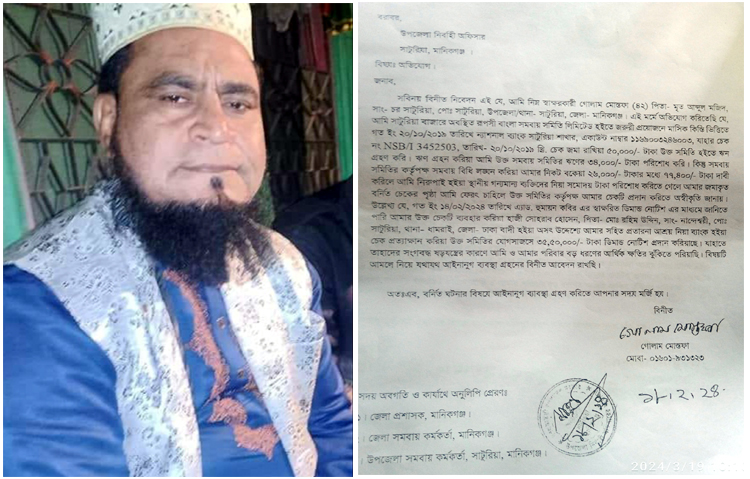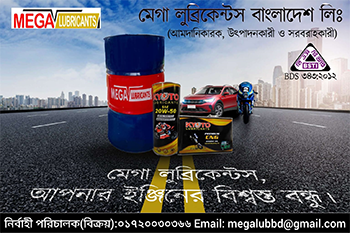- প্রকাশিত : ২০২৫-১১-০৩
- ৪৭ বার পঠিত

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
একটা সময় ছিল, মানুষ অসুস্থ হলে সব দায় ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিত। তখন চিকিৎসা ছিল সীমিত, বিজ্ঞান ছিল কেবল কৌতূহলের জায়গায়। চিকিৎসকও ছিলেন অসহায়—ওষুধের জ্ঞান সীমিত, প্রযুক্তির ছোঁয়া অল্প। রোগ সারলে বলা হতো ভাগ্য ভালো, না সারলে বলা হতো—ভাগ্যে ছিল না। কিন্তু যুগ পাল্টেছে। বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতিতে চিকিৎসা আজ পৌঁছে গেছে নতুন উচ্চতায়। রোগ নির্ণয় হয় মিনিটে, অস্ত্রোপচার হচ্ছে রোবটের হাতে, আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন অনেক সময় চিকিৎসকের সহকারী হয়ে কাজ করছে। এক সময় যে রোগকে মৃত্যুদণ্ড মনে করা হতো, আজ তারও চিকিৎসা সম্ভব। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এতো উন্নতির পরও এক অদ্ভুত শূন্যতা তৈরি হয়েছে—এক গভীর সংকট, যা প্রযুক্তি নয়, মানবতার।
চিকিৎসা আজ অনেকাংশে ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে, নৈতিকতার জায়গায় আসছে মুনাফার হিসাব, আস্থার জায়গায় আসছে সন্দেহ। চিকিৎসা কি এখন সেবার নাম, না কি পণ্যের নাম—এই প্রশ্ন আজ শুধু বাংলাদেশের নয়, গোটা বিশ্বের সামনে। হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার—সব জায়গাতেই এখন চলছে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা রোগীর সেবা দেওয়ার নয়, বরং বেশি লাভের। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরীক্ষা, অপ্রয়োজনীয় ওষুধ, কখনো অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার—সবই যেন মুনাফার সূত্রে বাঁধা। চিকিৎসার মানবিকতা ধীরে ধীরে পেছনে পড়ে যাচ্ছে।
অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিত্র আরেক রকম। সেখানেও সীমাহীন চাপ। এক ডাক্তারকে কখনো দিনে শতাধিক রোগী দেখতে হয়। পর্যাপ্ত বেড নেই, সাপোর্ট স্টাফ কম, যন্ত্রপাতি পুরোনো। অনেক সময় চিকিৎসকের চেয়ে রোগীর সংখ্যা এত বেশি হয় যে, প্রকৃত সেবা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যেখানে খরচ এমন যে মধ্যবিত্তের পক্ষে তা সামাল দেওয়া দুঃসাধ্য। রোগ সারানোর চেয়ে বিল মেটানোই যেন প্রধান লড়াই হয়ে উঠেছে। চিকিৎসা, যা এক সময় ছিল মানবসেবার প্রতীক, এখন যেন এক ব্যবসায়িক ব্যবস্থার অংশ।
প্রযুক্তি এই পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রেখেছে। চিকিৎসায় প্রযুক্তির আগমন নিঃসন্দেহে এক বিপ্লব। এখন রোগ শনাক্ত করা যায় কয়েক মিনিটে, রোবট অস্ত্রোপচার করে মিলিমিটার পরিমাণ নির্ভুলতায়, ভিডিও কলেই দূরের রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ পান। কিন্তু এই সুবিধার ভেতরেই এক ধরনের শীতলতা ঢুকে পড়েছে। এক সময় ডাক্তার রোগীর সঙ্গে কথা বলতেন, তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে রোগ বোঝার চেষ্টা করতেন। সেই উষ্ণ সম্পর্ক এখন অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে। রিপোর্ট, স্ক্যান, মেশিন—সবই হয়ে উঠেছে চিকিৎসার কেন্দ্রবিন্দু। রোগীর কথার চেয়ে মেশিনের প্রিন্টআউট বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। চিকিৎসা হচ্ছে নিখুঁত, কিন্তু ঠান্ডা।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে যন্ত্রপাতির অপব্যবহার। অনেক হাসপাতালে উন্নত প্রযুক্তি আনা হলেও প্রশিক্ষিত জনবল নেই। ফলে যন্ত্রটা আছে, কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না। রোগীকে দেওয়া হয় বাড়তি বিল, কিন্তু তার ফল মেলে সামান্য। প্রযুক্তি তখন চিকিৎসার আশীর্বাদ না হয়ে এক শীতল প্রতারণায় পরিণত হয়।
কোভিড–১৯ মহামারি এই চিত্রকে আরও নগ্ন করে দিয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম চিকিৎসা মানেই হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ। কিন্তু মহামারি দেখিয়ে দিয়েছে, এর চেয়ে অনেক গভীর প্রস্তুতির প্রয়োজন। অক্সিজেনের ঘাটতি, বেড সংকট, চিকিৎসকদের সুরক্ষা উপকরণের অভাব—সবকিছুই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে কতটা দুর্বল আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা। বহু মানুষ কেবল চিকিৎসা না পেয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা আমাদের শেখায়, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা না গড়ে তুললে ভবিষ্যতের যে কোনো মহামারি আমাদের আবার বিপর্যস্ত করবে।
আজ চিকিৎসা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সংকটের জায়গা হলো বিশ্বাস। একসময় ডাক্তার মানেই ছিল অগাধ আস্থা। রোগী তার কথা নিঃশর্তভাবে মেনে নিত। কিন্তু এখন সেই আস্থার জায়গায় এসেছে সন্দেহ। ইন্টারনেটের যুগে “ডাক্তার গুগল” এখন ঘরে ঘরে। রোগী নিজেই আগে থেকে পড়ে আসে, নানা ওষুধের নাম মুখস্থ করে নেয়, চিকিৎসকের পরামর্শকে চ্যালেঞ্জ করে। আবার কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত বিল, ভুল চিকিৎসা বা অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা—এসব ঘটনাও সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহিত করছে। ফলে চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক অদৃশ্য দেয়াল। অথচ চিকিৎসা শুধু ওষুধ বা অপারেশন নয়; এটি বিশ্বাস, সহানুভূতি ও মানবিকতার বন্ধন। সেই বন্ধন দুর্বল হয়ে গেলে চিকিৎসার আত্মা হারিয়ে যায়।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার ঘাটতি। প্রতিবছর দেশে হাজারো নতুন চিকিৎসক তৈরি হলেও, তাদের অনেকেই বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান না। অনেক মেডিকেল কলেজে গবেষণা কার্যক্রম নেই বললেই চলে। পাঠ্যক্রম এখনও অনেকাংশে মুখস্থ নির্ভর, যেখানে চিন্তা, বিশ্লেষণ, নৈতিকতা বা মানবিকতার শিক্ষা খুব কম। উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসা শিক্ষা গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত; নতুন তথ্যের অনুসন্ধান সেখানে চিকিৎসার অপরিহার্য অংশ। কিন্তু আমাদের দেশে সেই সংস্কৃতি এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রযুক্তি থাকলেও চিন্তা অনুপস্থিত থেকে যায়।
অ্যান্টিবায়োটিকের অতিব্যবহার আজ আরেক ভয়ংকর হুমকি। সামান্য জ্বর বা ঠান্ডা লাগলেই মানুষ নিজের মতো করে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করে দেয়। অনেক সময় প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ফার্মেসি থেকে ওষুধ বিক্রি হয়। ফলে জীবাণুগুলো ধীরে ধীরে প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই একে ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যদি এখনই নিয়ন্ত্রণ না আনা যায়, তবে এমন সময় আসবে, যখন সাধারণ সংক্রমণও মৃত্যু ডেকে আনবে।
এর পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও আজ বড় এক অবহেলিত বাস্তবতা। প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, মানুষ তত একা হয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক চাপ, পারিবারিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক প্রতিযোগিতা—সব মিলিয়ে মানুষ এখন এক গভীর মানসিক ক্লান্তিতে ভুগছে। বাংলাদেশের মতো দেশে কোটি কোটি মানুষ মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হলেও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আছেন হাতে গোনা। অথচ মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন না নিলে কোনো জাতিই প্রকৃত অর্থে সুস্থ হতে পারে না। আমাদের সমাজে এখনো মানসিক রোগ নিয়ে কথা বলা যেন লজ্জার বিষয়। এই সংস্কার না ভাঙলে চিকিৎসার এক বড় অংশ অপূর্ণই থেকে যাবে।
চিকিৎসা ব্যবস্থার আরেক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নৈতিকতা ও আইনি জটিলতা। চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসা কিংবা রোগীর অধিকার লঙ্ঘন—এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রতিনিয়ত। অনেক সময় দেখা যায়, রোগীর পক্ষ থেকে অযৌক্তিক অভিযোগ বা মামলা চিকিৎসকদের আতঙ্কিত করে তোলে। আবার কোথাও কোথাও চিকিৎসকদেরও ভুল আচরণ বা অবহেলা রোগীর ক্ষতির কারণ হয়। এই দুই চরমের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। চিকিৎসা হতে হবে দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও মানবিকতার ভিত্তিতে। রোগীর অধিকার যেমন রক্ষা করতে হবে, চিকিৎসকের মর্যাদাও তেমনি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।
ভবিষ্যতের চিকিৎসা হবে আরও প্রযুক্তিনির্ভর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক সার্জারি, জিন থেরাপি, বায়োপ্রিন্টিং—সবই নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, চিকিৎসার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ। মেশিন যতই শক্তিশালী হোক, মানুষের চোখের মায়া, সহানুভূতির হাত, কথা বলার সান্ত্বনা—এই অনুভূতিগুলো কোনো যন্ত্র দিতে পারে না। যদি আমরা মানবিক স্পর্শ হারাই, তবে চিকিৎসা নিছক একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে। তাই ভবিষ্যতের চিকিৎসা হতে হবে মানবিক প্রযুক্তিনির্ভর—যেখানে প্রযুক্তি হবে সহায়ক, কিন্তু নিয়ন্ত্রণে থাকবে মানুষ।
আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান একদিকে অগ্রগতির শীর্ষে, অন্যদিকে মানবিকতার পরীক্ষায়। আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ওষুধ তৈরি করেছি, কিন্তু বিশ্বাস কমিয়ে ফেলেছি। রোগী, চিকিৎসক ও সমাজ—তিন পক্ষের মধ্যকার সম্পর্ক এখন অনেকটাই দুর্বল। তাই আজ প্রয়োজন নতুন চিন্তার, নতুন নীতির। চিকিৎসাকে ফিরিয়ে আনতে হবে তার মূল জায়গায়—মানবসেবার জায়গায়।
চিকিৎসককে হতে হবে জ্ঞানী ও সহানুভূতিশীল, রোগীকে হতে হবে সচেতন ও সহযোগী, আর রাষ্ট্রকে দিতে হবে একটি ন্যায্য, সাশ্রয়ী ও কার্যকর স্বাস্থ্যব্যবস্থা। চিকিৎসা কেবল বিজ্ঞান নয়, এটি মানবতারই এক রূপ। রোগ সারানোই চিকিৎসার শেষ লক্ষ্য নয়; মানুষের পাশে দাঁড়ানোই চিকিৎসার প্রকৃত সার্থকতা। যদি আমরা সেই মানবিক মানসিকতা ফিরে পেতে পারি, তাহলে আজকের চ্যালেঞ্জই হবে আগামীর অনুপ্রেরণা।
লেখক, গবেষক ও জনস্বাস্থ্য বিশ্লেষক
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি